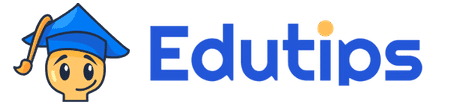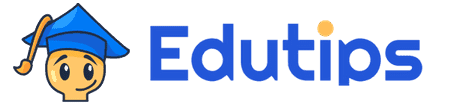উচ্চ মাধ্যমিক চতুর্থ সেমিস্টারের নতুন সিলেবাসে বাংলা প্রথম ভাষা গুরুত্বপূর্ণ গল্প পাঠ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদ পোড়া’ – ছোট গল্পটি। আজকের ক্লাসে আমরা এটি নিয়েই সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করব – তোমাদের সুবিধার জন্য বলে দিয়ে থাকি গল্প থেকে তোমাদের ৫ নম্বরের একটি বড় প্রশ্ন আসবে। আজকের এই ক্লাসের নোটগুলি ভালোভাবে ফলো করলে, তোমরা এই পাঁচ নম্বর খুব সহজেই পেয়ে যাবে।
সবার প্রথমে তোমাদেরকে পাঠের গল্পটি অবশ্যই ভালো করে একবার রিডিং পড়তে হবে, এটি একটি ভৌতিক গল্প – তাই অবশ্যই তোমাদের পড়তেও ভালো লাগবে – গল্পটা ভালো করে পড়া হয়ে গেলে তারপর এই নোটস বা প্রশ্ন উত্তর আলোচনাগুলো দেখলে বেশি কার্যকরি হবে। সবার প্রথমে আমরা লেখক পরিচিতি আলোচনা করব, তারপর বিষয়বস্তু, নামকরণের সার্থকতা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।
‘হলুদ পোড়া’ – মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (লেখক পরিচিতি)
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী বাঙালি কথাসাহিত্যিক। তাঁর প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তবে তিনি মানিক ডাকনামেই পরিচিত ছিলেন।
তিনি ১৯০৮ সালের ১৯ মে বর্তমান ভারতের ঝাড়খণ্ডের দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের নিকট মালবদিয়া গ্রামে। পিতা ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা।
ছাত্রজীবনে তিনি গণিত বিষয়ে পড়াশোনা করলেও বন্ধুদের সাথে বাজি ধরে লেখা তাঁর প্রথম গল্প ‘অতসী মামী’ ১৯২৮ সালে ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।
তিনি বাংলা সাহিত্যে মানুষের অন্তর্জীবন, মনোলোক বিশ্লেষণ এবং সমাজ বাস্তবতার অনুসন্ধানে শক্তিমত্তা দেখিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ এবং ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ অন্যতম।
‘হলুদ পোড়া’ তাঁর রচিত একটি ছোটগল্প, যা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে (১৩৫২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল।
‘হলুদ পোড়া’ সম্পূর্ণ গল্পের বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত সার)
গল্পের শুরু হয় কার্তিক মাসে হঠাৎ ঘটে যাওয়া দুটো খুনের ঘটনাকে ঘিরে। প্রথমে খুন হন বলাই চক্রবর্তী—তিনি ছিলেন এক মধ্যবয়স্ক/মাঝ-বয়সি যোয়ান মদ্দ পুরুষ। তিন দিন পর খুন হয় শুভ্রা, ষোল-সতের বছরের এক ভীরু স্বভাবের মেয়ে। এই দুটি মৃত্যুর মধ্যে সম্পর্ক কী?—তা নিয়ে গোটা গ্রাম জুড়ে নানা গুজব, সন্দেহ ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়। শুভ্রার বিবাহ হয়ে গিয়েছিল এবং বছর দেরেক সে তার শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। পরে সাত মাসের গর্ভবতী অবস্থায় সে বাপের বাড়ি আসে, তার দাদা ধীরেন চাটুয্যের কাছে, ধীরেনের স্ত্রী ছিলেন শান্তি। আর বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো নবীন চক্রবর্তী বলাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। নবীনের স্ত্রী ছিলেন দামিনী।
গ্রামের বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে কেউই গুরুতর যখন হয়নি সেইখানে পরপর দু’দুটো খুন হয়ে গেছে। শুভ্রার মৃত্যুর পর পাড়ায় নানা গুজব ছড়াতে থাকে। একুশ দিন পর, এক সন্ধ্যায় দামিনীর ওপর শুভ্রার অশরীরী আত্মা ভর করে। তখন নামকরা গুণী কুঞ্জকে ডেকে আনা হয়। কুঞ্জ যখন কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে তার নাকের কাছে ধরেন, তখন দামিনীর কণ্ঠে শোনা যায় শুভ্রার স্বীকারোক্তি— “আমি শুভ্রা.. আমায় মেরো না… বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।”
কিন্তু সমস্যা হলো—বলাই তো শুভ্রার খুনের তিন দিন আগেই মারা গেছে! ফলে রহস্য আরও গভীর হয়। দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রার আত্মা বলাই চক্রবর্তীর নাম করলে গ্রামে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। বুড়ো ঘোষাল ব্যাখ্যা করে—শুধু জ্যান্ত মানুষ গলা টিপে মারে না, অশরীরীরাও মাঝে মাঝে ক্ষতি করতে পারে। তবে কুঞ্জ গুণীর মতে, মরার পর এক বছরের মধ্যে সরাসরি মানুষ খুন করা সম্ভব নয়; তাই বলাই কারো শরীরে ভর করেই শুভ্রাকে খুন করেছে।
এইসব কথাবার্তা দ্রুত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরেনও গুজবগুলো শোনে, কিন্তু নিজের বোনের কেলেঙ্কারির কথা বারবার শুনে সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। অগ্রহায়ণের রোদেলা দিনে, ঘাটে শুভ্রার ওঠা–নামার জন্য বানানো ধাপ, ডোবার ধারে কচুরিপানা আর চারদিকের দৃশ্য দেখে ধীরেনের মনে নানা ভাবনা জাগে। ক্ষোভ ও দুঃখে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।
শান্তি (ধীরেনের স্ত্রী) একসময় নিজের ধারণা প্রকাশ করলে ধীরেন তাকে ধমক দেয়। চারপাশের মানুষ তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়, এমনকি স্কুলের হেডমাস্টারও তাকে এক মাসের ছুটি নিতে বলেন। এতে ধীরেন আরও ভেঙে পড়ে, নিজেকে একঘরে মনে হয়।
ধীরেন বাড়ি ফিরে আসে এবং সারাদিন মানসিক অস্থিরতায় কাটায়। সন্ধ্যা নামতেই ভয় আরও বাড়তে থাকে। শান্তি ছেলেমেয়েদের ঘরে আটকে রাখে, এমনকি ধীরেনকেও একা বাইরে যেতে মানা করে। তাদের ভয়ের পরিবেশ এত প্রবল হয় যে অল্পতেই শান্তি আঁতকে ওঠে—একবার পেঁচার ডাক শুনে সে ভয় পেয়ে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে বমি করে ফেলে।
এরপর ক্ষেন্তি পিসির কথামতো একটি নতুন বাঁশ কেটে, তার আগা–মাথা পুড়িয়ে আড়াআড়িভাবে ঘাটের পথে ফেলে রাখা হয়। বিশ্বাস ছিল, অশরীরী এই বাঁশ পার হতে পারবে না। ফলে শুভ্রা যদি ঘাট থেকে বাড়ির দিকে আসতেও চায়, সে বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকবে।
শান্তি সন্ধ্যার আগে সমস্ত ঘরের কাজ সেরে নেয়, তাড়াহুড়ো করে প্রদীপ জ্বালে, শাঁখ বাজায়, এমনকি রান্না-বাসনের ধরনও বদলে ফেলে—যেমন মাছ রান্না বন্ধ করে দেয়, কারণ এটোকাঁটা নাকি অশরীরীকে টানে।
ঘরে বন্দী হয়ে ধীরেন অস্থিরভাবে চিন্তায় ডুবে থাকে। সন্তানদের কথাবার্তায়ও ভয়ের ছাপ দেখা যায়—তারা বলে, “ছোটপিসি ভূত হয়েছে।” ধীরেন বলে, “ভূত নয়, পেত্নী।”
এইভাবে ধীরেন ও তার পরিবারের দিনযাপন ভয়ে-আতঙ্কে কাটতে থাকে। সন্ধ্যা নামলেই ঘরে আতঙ্ক আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা থেকে ধীরেনের পরিবারের কারও ওই আগা–মাথা পুড়িয়ে আড়াআড়িভাবে ঘাটের পথে ফেলে রাখা বাঁশ ডিঙ্গিয়ে বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু একদিন আকাশে তখনও শেষ আলো মিলিয়ে যায়নি, ধীরেন ভাবে—জীবিত ও মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হলো সন্ধ্যা। ভরসন্ধ্যাতেই যেহেতু শুভ্রা দামিনীকে ভর করেছিল, তাই ধীরেন মনে করে তার সঙ্গে শুভ্রার কথা বলার সুযোগ দেওয়া/পাওয়া উচিত। এই ভেবেই সে বাঁশ ডিঙ্গিয়ে মাঠের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ শোনা যায় হিংস্র জন্তুর গর্জনের মতো আওয়াজ। শান্তি তখন বলে ওঠে— “বাঁশটা ডিঙ্গিয়ে চলে এসো! পড়ে গেছো নাকি?”, ধীরেন উত্তর দেয়— “ডিঙ্গোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।” এরপর ধীরেন তীক্ষ্ণ গলায় আর্তনাদ শুরু করে। শান্তি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে যায় যে কোনো অশরীরী শক্তি তাকে ভর করেছে।
তখন চারদিক থেকে গ্রামের লোকজন জড়ো হয়। আসে গুণী কুঞ্জ। মন্ত্রপাঠ, আগুনে শিকড়-পাতা পোড়ানো আর ঘণ্টাখানেকের চেষ্টা শেষে তিনি ধীরেনকে শান্ত করতে সক্ষম হন। এরপর কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকে ধরে তুই কে? জিজ্ঞাসা করলে ধীরেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে আসল সত্য— “আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।” অর্থাৎ, ওই সন্ধ্যা বেলাতে বলাই চক্রবর্তীর অশরীরী আত্মা বা ভূত ধীরেনের উপর ভর করে।
‘হলুদ পোড়া’ গল্পের মুখ্য চরিত্র আলোচনা
বলাই চক্রবর্তী → এক মধ্যবয়স্ক/মাঝ-বয়সি যোয়ান মদ্দ পুরুষ, যার প্রথম খুন হয়। তার অশরীরী আত্মা পরে ধীরেনের উপর ভর করে এবং সে নিজেই স্বীকার করে—“আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।” কুঞ্জ গুণীর মতে, সরাসরি খুন করার ক্ষমতা মরার এক বছরের মধ্যে জন্মায় না; তাই বলাই অন্য কাউকে ভর করেই শুভ্রাকে খুন করেছে।
শুভ্রা → ষোল-সতের বছরের এক ভীরু স্বভাবের মেয়ে। শুভ্রার বিবাহ হয়ে গিয়েছিল এবং বছর দেরেক সে তার শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। পরে সাত মাসের গর্ভবতী অবস্থায় সে বাপের বাড়ি আসে, তার দাদা ধীরেন চাটুয্যের কাছে। বলাই চক্রবর্তী খুনের তিনদিন পরেই শুভ্রা খুন হয়, এবং পরবর্তীতে এক সন্ধ্যায় নবীনের স্ত্রী দামিনীর ওপর শুভ্রার অশরীরী আত্মা ভর করে দামিনীর কণ্ঠে শোনা যায় শুভ্রার স্বীকারোক্তি— “আমি শুভ্রা.. আমায় মেরো না… বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।” তার মৃত্যুর পরে গ্রামে নানা গুজব ছড়ায়, ধীরেনের ছেলেমেয়েরা তাকে “ভূত বা পেত্নী” বলে উল্লেখ করে।
নবীন চক্রবর্তী → বলাই চক্রবর্তীর ভাইপো। বলাই খুন হওয়ার পরে তার সমস্ত সম্পত্তি নবীনের দখলে যায়। সে সহরের চল্লিশ টাকার চাকরী ছেড়ে সপরিবারে গাঁয়ে/গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকে।
দামিনী চক্রবর্তী → নবীনের স্ত্রী। এক ভর সন্ধ্যায় তার ওপর শুভ্রার অশরীরী আত্মা ভর করে। দামিনীর কণ্ঠে শোনা যায় শুভ্রার স্বীকারোক্তি— “আমি শুভ্রা.. আমায় মেরো না… বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।”
ধীরেন চাটুয্যে → শুভ্রার দাদা। ধীরেন গ্রামে একমাত্র ডাক্তার পাশ-না-করা, ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এসসি পাস করে সাত বছর গ্রামের/স্থানীয় স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছেন। শুভ্রার স্বীকারোক্তিতে সব দোষ এসে পড়ে ধীরেন চাটুয্যের ওপর, এবং তাকে ঘিরে গ্রামে নানা কটুক্তি শুরু হয়। ধীরে ধীরে ধীরেন গ্রামে অপমান ও ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে এবং গ্রামে একঘরে হয়ে পড়ে। একদিন আকাশে তখনও শেষ আলো মিলিয়ে যায়নি, তিনি ভাবে—জীবিত ও মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হলো সন্ধ্যা। ভরসন্ধ্যাতেই যেহেতু শুভ্রা দামিনীকে ভর করেছিল, তাই তিনি মনে করে তার সঙ্গে শুভ্রার কথা বলার সুযোগ দেওয়া/পাওয়া উচিত। সন্ধ্যাবেলায় বাঁশ ডিঙিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করে এবং তখন তার উপর বলাই চক্রবর্তীর আত্মা ভর করে।
শান্তি → ধীরেনের স্ত্রী। সবসময় ভয়-আতঙ্কে দিন কাটায়। সন্ধ্যার পর একা বাইরে বেরোয় না, ছেলেমেয়েকেও ঘরে আটকে রাখে। ক্ষান্তি পিসির পরামর্শে নতুন বাঁশ কেটে আগা-মাথা পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখে—যাতে অশরীরী আত্মা ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। শেষে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে বোঝে যে ধীরেনকে অশরীরী ভর করেছে।
কুঞ্জ → গ্রামের নামকরা গুণী। দামিনী ও পরে ধীরেনকে ভূতগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। মন্ত্রপাঠ, শিকড়-পাতা পোড়ানো, আগুনে জল ছিটানো এবং শেষে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে নাকে ধরার মাধ্যমে সত্য বের করে আনে।
কৈলাস ডাক্তার → এক বিশালকায় মানুষ, জমকালো চেহারা, মোটা ভুরু ও খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি, একমাথা কাঁচাপাকা চুল। ঘুমের ওষুধ বা চিকিৎসার প্রক্রিয়ায় পারদর্শী, কিন্তু রাগে সহজে উগ্র হয়ে ওঠে, গর্জন করতে ভালোবাসে এবং অন্যদের উপর আধিপত্য দেখায়।
ক্ষেন্তি পিসি → গ্রামের এক বৃদ্ধা মহিলা, যিনি উপায় বাতলে দেন বাঁশ কেটে আগা-মাথা পুড়িয়ে ঘাটের পথে ফেলে রাখতে। বিশ্বাস ছিল, কোনো অশরীরী এই বাঁশ ডিঙোতে পারবে না।
বুড়ো ঘোষাল → গ্রাম্য মানুষ। তিনি ব্যাখ্যা দেন—মরা মানুষও মাঝে মাঝে মানুষের ক্ষতি করতে পারে, এতে অনেকের সন্দেহ কেটে যায়। তবে তার ব্যাখ্যা কুঞ্জ গুণীকে ঘুরিয়ে সমর্থন করতে হয়, নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য।
পুরোহিত (পুরুতঠাকুর) → গ্রামের পুরোহিত। তিনি ধীরেনকে দোষমোচনের জন্য ক্রিয়াকর্ম করার পরামর্শ দেন এবং মাদুলি ধারণ করার নির্দেশ দেন।
মথুরবাবু → স্কুলের সেক্রেটারি। তিনিই হেডমাস্টারকে বলেন ধীরেনকে এক মাসের ছুটি দিতে।
সম্পর্ক
বলাই চক্রবর্তী (কাকা) → নবীন চক্রবর্তী (ভাইপো)
দামিনী → নবীনের স্ত্রী, অর্থাৎ বলাইয়ের ভাইপোর বউ।
শুভ্রা (বোন) → ধীরেন চাটুয্যে (দাদা)
শান্তি → ধীরেনের স্ত্রী, অর্থাৎ শুভ্রার ভ্রাতৃবধূ।
‘হলুদ পোড়া’ গল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর আলোচনা।
নিচে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া হলো – যেগুলি সরাসরি তোমাদের পরীক্ষাতে আসতে পারে, পরীক্ষাতে আংশিক বা লাইন তুলে উক্তি হিসেবে প্রশ্ন আসতে পারে – নিচের উত্তরটি ভালো করে করে গেলে যে কোন প্রশ্ন আসুক তোমরা কিন্তু লিখে আসতে পারবে। আর উপরের বিষয়বস্তু তাতে তোমরা ভালো করে পড়ে যাচ্ছো চরিত্রের নাম গুলো করে যাচ্ছ কাজে কোন রকম অসুবিধা হবে না।
প্রশ্ন: ছোট গল্প হিসেবে ‘হলুদ পোড়া’ গল্পটি কতদূর সার্থক তা নিজের ভাষায় আলোচনা কর। ★★★ সংসদ নমুনা প্রশ্ন
অথবা, ‘হলুদ পোড়া’ ছোট গল্পটির ‘নামকরণের সার্থকতা‘ বিশ্লেষণ কর। ★
➤ উত্তর ➨ বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘হলুদ পোড়া’ গল্পটি বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এটি একদিকে লোক-কথা মূলক গল্প আবার অন্যদিকে ভৌতিক আবহে মোড়ানো, যেখানে গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার, রহস্য, ভয় এবং মানুষের মনস্তত্ত্ব/মানসিকতা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
গল্পের শুরু হয় কার্তিক মাসে হঠাৎ ঘটে যাওয়া দুটো খুনের ঘটনাকে ঘিরে। প্রথমে খুন হন বলাই চক্রবর্তী—তিনি ছিলেন এক মধ্যবয়স্ক/মাঝ-বয়সি যোয়ান মদ্দ পুরুষ। তিন দিন পর খুন হয় শুভ্রা, ষোল-সতের বছরের এক ভীরু স্বভাবের মেয়ে। এই দুটি মৃত্যুর মধ্যে সম্পর্ক কী?—তা নিয়ে গোটা গ্রাম জুড়ে নানা গুজব, সন্দেহ ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়। শুভ্রার বিবাহ হয়ে গিয়েছিল এবং বছর দেরেক সে তার শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। পরে সাত মাসের গর্ভবতী অবস্থায় সে বাপের বাড়ি আসে, তার দাদা ধীরেন চাটুয্যের কাছে, ধীরেনের স্ত্রী ছিলেন শান্তি। আর বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো নবীন চক্রবর্তী বলাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। নবীনের স্ত্রী ছিলেন দামিনী।
গ্রামের বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে কেউই গুরুতর যখন হয়নি সেইখানে পরপর দু’দুটো খুন হয়ে গেছে। শুভ্রার মৃত্যুর পর পাড়ায় নানা গুজব ছড়াতে থাকে। একুশ দিন পর, এক সন্ধ্যায় দামিনীর ওপর শুভ্রার অশরীরী আত্মা ভর করে। তখন নামকরা গুণী কুঞ্জকে ডেকে আনা হয়। কুঞ্জ যখন কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে তার নাকের কাছে ধরেন, তখন দামিনীর কণ্ঠে শোনা যায় শুভ্রার স্বীকারোক্তি— “আমি শুভ্রা.. আমায় মেরো না… বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।”
কিন্তু সমস্যা হলো—বলাই তো শুভ্রার খুনের তিন দিন আগেই মারা গেছে! ফলে রহস্য আরও গভীর হয়। বুড়ো ঘোষাল বলে যে, বলাই হয়তো কোনো জীবিত মানুষকে ভর করে শুভ্রাকে খুন করেছে। শুভ্রার এই স্বীকারোক্তিতে তখন সব দোষ এসে পড়ে ধীরেন চাটুয্যের ওপর, এবং তাকে ঘিরে গ্রামে নানা কটুক্তি শুরু হয়। ধীরে ধীরে ধীরেন গ্রামে অপমান ও ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে এবং গ্রামে একঘরে হয়ে পড়ে।
এরপর গল্পের মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ক্ষেন্তি পিসি পরামর্শ দেয় যে একটি নতুন বাঁশ কেটে তার আগা ও মাথা পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখতে। কারণ কোনো অশরীরী সেই বাঁশ পার করতে পারবে না। সন্ধ্যা থেকে ধীরেনের পরিবারের কারও ওই বাঁশ ডিঙ্গিয়ে বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু একদিন আকাশে তখনও শেষ আলো মিলিয়ে যায়নি, ধীরেন ভাবে—জীবিত ও মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হলো সন্ধ্যা।
ভরসন্ধ্যাতেই যেহেতু শুভ্রা দামিনীকে ভর করেছিল, তাই ধীরেন মনে করে তার সঙ্গে শুভ্রার কথা বলার সুযোগ দেওয়া/পাওয়া উচিত। এই ভেবেই সে বাঁশ ডিঙ্গিয়ে মাঠের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ শোনা যায় হিংস্র জন্তুর গর্জনের মতো আওয়াজ। শান্তি তখন বলে ওঠে— “বাঁশটা ডিঙ্গিয়ে চলে এসো! পড়ে গেছো নাকি?”, ধীরেন উত্তর দেয়— “ডিঙ্গোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।” এরপর ধীরেন তীক্ষ্ণ গলায় আর্তনাদ শুরু করে। শান্তি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে যায় যে কোনো অশরীরী শক্তি তাকে ভর করেছে।
তখন চারদিক থেকে গ্রামের লোকজন জড়ো হয়। আসে গুণী কুঞ্জ। মন্ত্রপাঠ, আগুনে শিকড়-পাতা পোড়ানো আর ঘণ্টাখানেকের চেষ্টা শেষে তিনি ধীরেনকে শান্ত করতে সক্ষম হন। এরপর কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকে ধরে তুই কে? জিজ্ঞাসা করলে ধীরেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে আসল সত্য— “আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।” অর্থাৎ, ওই সন্ধ্যা বেলাতে বলাই চক্রবর্তীর অশরীরী আত্মা বা ভূত ধীরেনের উপর ভর করে।
অতএব, গল্পের শুরুতেও রহস্য উন্মোচনে ‘হলুদ পোড়া’ ব্যবহৃত হয়েছে, আবার শেষেও খুনের আসল রহস্য উদঘাটনে এই ‘হলুদ পোড়া’ই ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এ সবই লোকবিশ্বাস-কুসংস্কার, তবুও এই কুসংস্কার-বিশ্বাসকেই লেখক গল্পের ভৌতিক আবহকে আরও দৃঢ় ও বাস্তব করে তুলতে নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন।
সব মিলিয়ে বলা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লোক-কথা মূলক ভৌতিক ছোটগল্পে ‘হলুদ পোড়া’ নামকরণ অত্যন্ত সার্থক। গল্পটি রহস্য, ভয় ও কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে পাঠকের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, এবং সার্থক ছোটগল্পের সব গুণ এতে বিদ্যমান।
‘হলুদ পোড়া’ গল্পে “বাঁশ” প্রতীকের তাৎপর্য কী? লেখক কেন এটিকে অশরীরীর বাধা হিসেবে দেখিয়েছেন?
➤ উত্তর ➨ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘হলুদ পোড়া’ গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের জগতে ভৌতিক ও লোককথা নির্ভর সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এখানে গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার, রহস্য এবং মানুষের মানসিকতা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
গল্পে ‘বাঁশ’ শুধুমাত্র একটি উদ্ভিদ নয়, বরং এটি কুসংস্কার ও ভয়ের প্রতিরক্ষামূলক বর্ম বা বিশ্বাস ও বাস্তবতার মধ্যে সীমারেখা হিসেবে কাজ করেছে। বাঁশ প্রতীক মূলত সীমানা ও রোধ নির্দেশ করে; জীবিতদের নিরাপত্তা ও অশরীরী অনুপ্রবেশ ঠেকানোর এক চিহ্ন।
➨ শুভ্রার দাদা ধীরেন যখন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং তাঁর স্ত্রী শান্তি যখন আতঙ্কে জীবন যাপন করেন, তখন ‘ক্ষেন্তি পিসি’র পরামর্শে একটি কাঁচা বাঁশ কেটে, তার আগা-মাথা পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখা হয়। গ্রামীণ লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, অশরীরী আত্মা বা প্রেতাত্মা পোড়া বাঁশ ডিঙিয়ে বা পার হয়ে বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। লেখক শৈলীতে বাঁশকে শুধু বস্তু না রেখে মানবসমাজের নিরাপত্তা-চিন্তার প্রতীক বানিয়েছেন—যেখানে মানুষের ভীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস মিলে অদেখা বিপদ সামলায়। ধীরেন যখন বাঁশ ডিঙিয়ে মাঠে যায় এবং চিৎকার করে “ডিঙ্গোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।”, তখন বাঁশের প্রতিরোধ কেবল ভৌত নয়, মানসিক ভাঙন ও সামাজিক নৈতিকতার রোধও দেখায়।
বাঁশটি যেন ধীরেনের মনের সেই গোপন দেওয়াল, যা তিনি স্বেচ্ছায় তৈরি করেছিলেন অপরাধবোধ থেকে বাঁচতে। কিন্তু যখন অপরাধী আত্মা (বলাই) তাঁকে ভর করে, তখন সেই বাধা বাস্তব হয়ে ওঠে। সুতরাং, বাঁশ প্রতীকীভাবে গ্রামীণ বিশ্বাসের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে, যা বিজ্ঞানের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রতীকিক ব্যবহার পাঠককে গ্রামীণ নৈতিকতা ও ভয়াবহতার মনস্তত্ত্বে নিয়ে যায় এবং কাহিনীর আবহকে আরও ঘনীভূত করে; এতে সামাজিক আচার–প্রথার দ্বন্দ্বও প্রকাশ পায়।
“জীবিত ও মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হলো সন্ধ্যা।” — উক্তিটি গল্পে কী প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে? এর মাধ্যমে ধীরেনের মানসিক অবস্থার পরিচয় কীভাবে পাওয়া যায়?
➤ উত্তর ➨ প্রখ্যাত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা এই ‘হলুদ পোড়া’ গল্পের মাধ্যমে যুক্তিবাদের পতন ও লোকবিশ্বাসের তীব্র প্রভাব তুলে ধরেছেন। গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের জগতে ভৌতিক ও লোককথা নির্ভর সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। প্রশ্নে আলোচ্য উক্তিটি ছিল শুভ্রার দাদা, ধীরেন চাটুয্যে-র চরম মানসিক অস্থিরতা ও আত্ম-ধ্বংসাত্মক প্রবণতার প্রকাশ।
বলাই চক্রবর্তী এবং শুভ্রা খুনের রহস্যে গ্রাম যখন কুসংস্কার ও গুজবে আচ্ছন্ন, তখন নবীনের স্ত্রী দামিনীর উপর ভর করে শুভ্রার আত্মা জানায়, তাকে বলাই খুন করেছে। এতে ধীরেন সমাজে অপমান ও ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে পড়েন, তাঁর মনের মধ্যে “ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য” জমে ওঠে। প্রথমবার শুভ্রা ভর করেছিল ভর সন্ধ্যাবেলায়। ধীরেন তখন যুক্তির পথ ছেড়ে হতাশায় ডুবে গিয়ে ভাবেন, “জীবিত ও মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হলো সন্ধ্যা।” তিনি মনে করেন, “আর দেরী না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।” এই ভেবে তিনি অশরীরীর বাধা হিসেবে রাখা পোড়া বাঁশ ডিঙিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে যান।
➨ ফিজিক্সে অনার্স পাশ করা ধীরেনের এই উক্তিটি তাঁর শিক্ষিত সত্তার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের পরিচয় বহন করে। কুসংস্কারকে ‘দুর্বুদ্ধি’ বলা মানুষটি যখন নিজের বোনের ‘পেত্নী’ রূপের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চান, তখন বোঝা যায় তাঁর মনের যুক্তির দেওয়াল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। এই উক্তি এক প্রকার মৃত্যুকামিতা প্রকাশ করে, যেখানে তিনি নিজেই রহস্যের উন্মোচন বা মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন।
শেষ পর্যন্ত, অশরীরী (বলাই) তাঁকে ভর করলে তিনি সেই পোড়া বাঁশের কাছে এসে আটকে গিয়ে আর্তনাদ করেন—“ডিঙ্গোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।” এই ঘটনা প্রমাণ করে, ধীরেন তখন আর যুক্তিমান মানুষ নন, বরং কুসংস্কারের প্রতীকী বাধায় আটকে পড়া এক আত্মা, যার মুখ দিয়েই চূড়ান্ত সত্যটি প্রকাশ পায়: “আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।”
“আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।” — এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে গল্পে কী নাটকীয় পরিণতি ঘটে?
➤ উত্তর ➨ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ‘হলুদ পোড়া’ গল্পের প্রধান নাটকীয়তা নিহিত রয়েছে ‘হলুদ পোড়া’ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত দ্বিতীয় স্বীকারোক্তিটির মধ্যে, যা গ্রামীণ বিশ্বাস ও খুনের রহস্যের চরম উন্মোচন ঘটায়। এই স্বীকারোক্তিটি ছিল ফিজিক্সে অনার্স পাশ করা শিক্ষিত ধীরেন চাটুয্যে-র মুখ দিয়ে, যখন গুণিন কুঞ্জ মাঝি হলুদ পুড়িয়ে নাকে ধরলে ধীরেনের উপর ভর করা আত্মাটি বলে ওঠে— “আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।” এই চরম নাটকীয়তার মাধ্যমে গল্পে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি আসে।
প্রথমত, এটি খুনের রহস্যের চূড়ান্ত সমাধান করে। প্রথমবার নবীনের স্ত্রী দামিনীর উপর ভর করে শুভ্রা জানায়— “আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা… বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।”, এই জবানবন্দিতে তখন একটি ধোঁয়াশা তৈরি হয়—কারণ বলাই শুভ্রার তিন দিন আগেই মারা গিয়েছিল। বুড়ো ঘোষাল ও কুঞ্জ গুণীর কুসংস্কারমূলক ব্যাখ্যায় এই রহস্য আরও জটিল হয়। কিন্তু গল্পের চরম নাটকীয়তা ঘটে দ্বিতীয়বার যখন ধীরেনের মুখ দিয়ে বলাইয়ের আত্মা যখন নিজের খুনের কথা স্বীকার করে, তখন আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে শুভ্রাকে সত্যিই বলাই চক্রবর্তী খুন করেছিল।
দ্বিতীয়ত, এই স্বীকারোক্তিটি গল্পের মনস্তাত্ত্বিক ও যুক্তিবাদী সত্তার পতনকে প্রতিষ্ঠা করে। ধীরেন প্রথমে কুঞ্জ মাঝির গুণপনাকে “ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন” বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অথচ, শেষ পর্যন্ত তাঁকেই এই অশরীরী প্রক্রিয়ার শিকার হতে হয়। তাঁর মুখ দিয়েই যখন বলাইয়ের আত্মা কথা বলে, তখন গ্রামীণ কুসংস্কারের কাছে যুক্তিবাদীর পরাজয় চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়। ধীরেনকে সেই পোড়া বাঁশের কাছে আটকে গিয়ে আর্তনাদ করতে হয়—“ডিঙ্গোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও”—যা তাঁর অবচেতন অপরাধবোধ এবং যুক্তির পতনকে একইসাথে চিহ্নিত করে। এই নাটকীয় পরিণতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রামীণ জীবন ও মানসিকতার একজন শক্তিশালী বিশ্লেষক হিসেবে তুলে ধরে।
শুভ্রার মৃত্যুর পর গ্রামে যে ভয় ও রহস্যের আবহ তৈরি হয়, তা কীভাবে মানুষের মনোজগতের অন্ধ বিশ্বাসকে প্রকাশ করে?
➤ উত্তর ➨ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা ‘হলুদ পোড়া’ গল্পে দুটি অস্বাভাবিক খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সমাজের মনোজগতে লুকিয়ে থাকা গভীর অন্ধ বিশ্বাসকে অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন।
শুভ্রা ছিল “গেরস্ত ঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে”, তাই তার খুন হওয়াতে “মানুষের বিস্ময় ও কৌতুহলের সীমা রইল না।” এই অস্বাভাবিক মৃত্যু গ্রামের মানুষের মধ্যে কোনো বাস্তব সত্যের খোঁজ না দিয়ে বরং অন্ধ বিশ্বাস ও গুজবের জন্ম দেয়। যখন নবীনের স্ত্রী দামিনীর ওপর ভর করে শুভ্রার আত্মা “বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে” বলে স্বীকারোক্তি দেয়, তখন এই রহস্য গ্রামীণ লোককথার স্তরে পৌঁছে যায়। মৃত বলাই কী করে খুন করতে পারে, সেই ধাঁধা সৃষ্টি হলে, বুড়ো ঘোষাল ও কুঞ্জ গুণী সহজেই ব্যাখ্যা দেয়— “শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না?” অর্থাৎ, অশরীরী আত্মা প্রতিশোধ নিতে পারে। এই যুক্তিহীন ব্যাখ্যাই সমস্ত গ্রাম গ্রহণ করে।
এই ঘটনাপ্রবাহ ধীরেনের স্ত্রী শান্তি এবং গ্রামের অন্যান্য মানুষের মনোজগতের অন্ধ বিশ্বাসকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। শান্তি ছোট বাচ্চাদের “ছোটপিসী ভূত হয়েছে” বা “ভূত নয়, পেত্নী” বলা শুনে ভয় পায় এবং অল্পতেই “আঁতকে ওঠে”। এই অন্ধ বিশ্বাস এত গভীর যে, সে যুক্তির পথ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে ক্ষেন্তি পিসির কথামতো “নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখে”, যাতে শুভ্রার অশরীরী আত্মা গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। এমনকি সে মাছ রান্না পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়, কারণ “এটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে।”
সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই অন্ধ বিশ্বাস গ্রামের শিক্ষিত মানুষটিকেও গ্রাস করে। ধীরেন চাটুয্যে, যিনি বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া সত্ত্বেও শেষে এই বিশ্বাস দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হন যে তিনি নিজেও সেই পোড়া বাঁশকে অশরীরীর বাধা হিসেবে দেখেন এবং “জীবিত ও মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হলো সন্ধ্যা” মনে করে নিজেই অশরীরীর মুখোমুখি হতে যান। এই সমস্ত ঘটনা প্রমাণ করে, গ্রামীণ রহস্যময় পরিবেশে যুক্তি বা বিজ্ঞান নয়, বরং প্রজন্ম ধরে চলে আসা গভীর অন্ধ বিশ্বাসই মানুষের মনোজগতের প্রধান চালক।
“বাঁশটা ডিঙিয়ে চলে এসো! পড়ে গেছো নাকি?” — এই সংলাপের মাধ্যমে গল্পে কোন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সূচনা ঘটে? ব্যাখ্যা করো।
➤ উত্তর ➨ প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা ‘হলুদ পোড়া’ ছোটগল্পে সমাজের কুসংস্কার, রহস্য এবং মানুষের মানসিকতা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।
প্রদত্ত সংলাপটি গল্পে রহস্যের চূড়ান্তে পৌঁছানো এবং যুক্তিবাদী ধীরেন চাটুয্যে-র চূড়ান্ত মানসিক পতনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সূচনা করে। এই মুহূর্তের পরেই গল্পে বলাই চক্রবর্তীর আত্মা ধীরেনকে ভর করে এবং খুনের আসল সত্য প্রকাশিত হয়।
➨ শুভ্রা খুনের পর তার দাদা ধীরেন যখন গ্রামে অপমানিত ও একঘরে হয়ে যান, তখন তিনি যুক্তির পথ ছেড়ে দিয়ে “জীবিত ও মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হলো সন্ধ্যা” মনে করে ডোবার ঘাটের দিকে যান, তখন তাঁর স্ত্রী শান্তি দেখেন যে তিনি “কাদা ও রক্ত মাখা” অবস্থায় আছেন এবং “হিংস্র জন্তুর চাপাগর্জনের মত গম্ভীর আওয়াজে” কথা বলছেন। শান্তি তখন স্বামীকে স্বাভাবিক মনে করে বলেন, “বাঁশটা ডিঙিয়ে চলে এসো! পড়ে গেছো নাকি?” কিন্তু ধীরেন বিকৃত গলায় উত্তর দেন— “ডিঙ্গোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।” এই উত্তর শুনে— “শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না” যে ধীরেনকে কোনো অশরীরী শক্তি ভর করেছে। এই সংলাপটি সেই মুহূর্তের সূচনা করে, যখন শান্তিসহ গ্রামের সকলে নিশ্চিত হয় যে শিক্ষিত ধীরেনের উপরও আত্মা ভর করেছে।
এই সংলাপের পরই গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে যায়, কুঞ্জ গুণী আসে এবং হলুদ পোড়ার প্রক্রিয়ায় ধীরেনের মুখ দিয়ে বলাইয়ের খুনের স্বীকারোক্তি বেরিয়ে আসে। অতএব, এই সংলাপটি ছিল মানবীয় যুক্তি থেকে অলৌকিক রহস্যের জগতে প্রবেশের একটি নাটকীয় দ্বার উন্মোচন।
গল্পে ধীরেন চাটুয্যের ওপর গ্রামবাসীর কটূক্তি ও অবিশ্বাস কিসের ইঙ্গিত দেয়?
➤ উত্তর ➨ বাংলা কথাসাহিত্যের বিখ্যাত লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্ব ও গ্রামীণ কুসংস্কারের বাস্তবানুগ চিত্রায়ণের জন্য তাঁর লেখা ‘হলুদ পোড়া’ ছোটগল্পে ভৌতিক ও লোককথা নির্ভর সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।
এই গল্পে ধীরেন চাটুয্যের ওপর গ্রামবাসীর কটূক্তি ও অবিশ্বাস মূলত গ্রামীণ সমাজের যুক্তির ওপর কুসংস্কারের কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তিগত মানহানির মাধ্যমে একঘরে করার প্রবণতাকে ইঙ্গিত করে।
➨ ধীরেন ছিলেন “ডাক্তার পাশ-না-করা,” ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এসসি পাশ করা একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি, যিনি প্রথমে নবীনের প্রতি উপদেশ দেন, “ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন। আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়!” অর্থাৎ, তিনি যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক। কিন্তু যখন নবীনের স্ত্রী দামিনীর ওপর শুভ্রার আত্মা ভর করে বলাইয়ের নাম নেয়, তখন গ্রামে গুজব ছড়ায় যে শুভ্রা চরিত্রহীনা ছিল এবং তার খুনের সঙ্গে বলাইয়ের সম্পর্ক ছিল। এই গুজব ধীরেনকে ঘিরে ব্যঙ্গের ও অবিশ্বাসের এক আবহ তৈরি করে। গ্রামবাসী তাঁকে এমনভাবে দেখতে শুরু করে যেন তিনি “যেন বাইরের কোন বিশিষ্ট অভ্যাগত স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে”—অর্থাৎ, তিনি আর তাদের সমাজের অংশ নন। এমনকি পুরোহিত তাঁকে দোষমোচনের জন্য “মাদুলী নিয়ে যায়”-এর নির্দেশ দেন, যা তাঁর যুক্তিবাদী অবস্থানকে বাতিল করে।
গ্রামের মানুষ শুভ্রার কথিত কেলেঙ্কারি এবং সেই সূত্রে ধীরেনকে কটূক্তি করে প্রকারান্তরে তাঁর সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানহানি করে। স্কুলের সেক্রেটারি মথুরবাবু তাঁকে “একমাসের ছুটি” নিতে বলেন। এই আচরণ ইঙ্গিত দেয় যে, গ্রামীণ সমাজ কোনো অপরাধ বা অস্বাভাবিক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেলে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত সততা ও শিক্ষাকে সহজেই বাতিল করে দেয়। ধীরেন নিজেই তখন লজ্জা ও অপমানে জর্জরিত হয়ে ওঠেন এবং “চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ী চলেছে।” গ্রামবাসীর এই সম্মিলিত অবিশ্বাস ধীরেনকে মানসিকভাবে এমনভাবে ভেঙে দেয় যে তিনি শেষে যুক্তি ত্যাগ করে অশরীরীর মুখোমুখি হতে যান। অর্থাৎ, সমাজই তাকে যুক্তির আলো থেকে ঠেলে ভয়ের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে, যেখানে কুসংস্কারই শেষ কথা।
গল্পে গুণী কুঞ্জের ভূমিকা কী? সে কীভাবে গল্পের উত্তেজনা প্রশমিত করে?
➤ উত্তর ➨ বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা ভৌতিক ও লোককথামূলক ‘হলুদ পোড়া’ ছোটগল্পে গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার, রহস্য এবং মানুষের মানসিকতার চমৎকার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। গল্পে গুণী কুঞ্জ মাঝি গ্রামীণ সমাজের লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূর্ত প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
➨ গল্পের প্রথমেই তিন দিন অন্তর ঘটে যাওয়া বলাই চক্রবর্তী ও শুভ্রার খুনের ঘটনার কয়েকদিন পর পর, যখন বলাই চক্রবর্তীর ভাইপো নবীনের স্ত্রী দামিনীর উপর শুভ্রার আত্মা ভর করে, তখন শিক্ষিত ধীরেন এটিকে অসুখ বললেও গ্রামের অধিকাংশ মানুষ “কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও” বলে সায় দেয়। কুঞ্জ এসে প্রথমেই ঘোষণা করে, “ভর সাঁঝে ভর করেছেন সহজে ছাড়বেন না!”—এর মাধ্যমে সে অলৌকিকতার ভীতিকে প্রতিষ্ঠা করে।
কুঞ্জ এসেই তার প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমিত করে। সে মন্ত্র পাঠ, জল ছিটানো, এবং চামড়া পোড়ার মতো উৎকট গন্ধে শুকনো পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে প্রথমে দামিনীকে বশে আনে। এরপর “কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে” তার নাকে ধরে শুভ্রার আত্মাকে কথা বলাতে বাধ্য করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে শুভ্রার খুনি হিসেবে বলাই চক্রবর্তীর নাম বের করে আনে। এবং পরবর্তীকালে ধীরেনকে যখন বলাইয়ের আত্মা ভর করে, তখনও কুঞ্জ তার পদ্ধতি অবলম্বন করে। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে নিঝুম করে সে হলুদ পোড়ার মাধ্যমে আসল সত্যটি বের করে আনে— “আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।” এই চরম স্বীকারোক্তিটিই গল্পের সমস্ত রহস্যের সমাধান করে।
কুঞ্জের এই পদ্ধতিগুলি গ্রামীণ মানুষকে এক বিরল “তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতুহল ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ” দেয়। গ্রামের মানুষ মনে করে, দাওয়ায় যেন “জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক” আমদানি হয়েছে। কুঞ্জ এই লোকবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ভয়ের পরিবেশকে একধরনের নাটকীয় প্রদর্শনীতে রূপান্তরিত করে, যেখানে সবাই একত্রিত হয়ে সমস্যার সমাধান দেখে। এর ফলে, খুনের বাস্তব রহস্যের পরিবর্তে অশরীরী শক্তির কার্যকলাপকেই মানুষ মেনে নেয় এবং সাময়িকভাবে সমাজে বিরাজ করা অস্থিরতা ও উত্তেজনা প্রশমিত হয়।
“ভর সন্ধ্যাবেলাতেই দামিনীকে শুভ্রা আশ্রয় করেছিল।” — এই ঘটনাটি গল্পের মূল রহস্য উন্মোচনে কী ভূমিকা পালন করে?
➤ উত্তর ➨ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘হলুদ পোড়া’ গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের জগতে ভৌতিক ও লোককথা নির্ভর সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এখানে গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার, রহস্য এবং মানুষের মানসিকতা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
গল্পের শুরুতে শুভ্রার খুনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, “গাঁয়ে সব শেষের সাঁঝের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে তখন বাড়ীর পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মত মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁ শুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল।” এই ‘সাঁঝের বাতিটি জ্বালার সময়’ বা ‘ভর সন্ধ্যাবেলা’র উল্লেখ গল্পের মূল রহস্য উন্মোচনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
প্রথমত, ‘ভর সন্ধ্যাবেলা’তেই নবীনের স্ত্রী দামিনীর ওপর শুভ্রার আত্মা ভর করে এবং গুণীন কুঞ্জের হলুদ পোড়া প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে আসে শুভ্রার স্বীকারোক্তি— “বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।” শুভ্রার আত্মা এই বিশেষ সময়েই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে গ্রামের মানুষের মনে নিশ্চিত ধারণা তৈরি করে যে এটি কোনো সাধারণ অসুস্থতা নয়, বরং অশরীরী শক্তির কার্যকলাপ। এই ঘটনাটিই গল্পের মনস্তাত্ত্বিক রহস্যের প্রধান সূত্রপাত ঘটায় এবং গ্রামের মানুষদের যুক্তির জগৎ থেকে কুসংস্কারের দিকে ঠেলে দেয়।
দ্বিতীয়ত, এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা ধীরেন চাটুয্যের যুক্তিবাদী মনকে গ্রাস করে ফেলে। তিনি তখন ভাবতে শুরু করেন— “জীবিত ও মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হলো সন্ধ্যা। ভর সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল।” এই বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয়েই তিনি “আর দেরী না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত” মনে করেন এবং নিজেই পোড়া বাঁশের বাধা ডিঙিয়ে অশরীরীর মুখোমুখি হতে যান। ফলে সেই ‘ভর সন্ধ্যাবেলা’র ঘটনাটি শিক্ষিত ধীরেনকে অন্ধ বিশ্বাসের পথে চালিত করে, যার ফলস্বরূপ তাঁর ওপর বলাই চক্রবর্তীর আত্মা ভর করে এবং দ্বিতীয় হলুদ পোড়ার মাধ্যমে ধীরেনের মুখে আসল সত্যটি প্রকাশিত হয়— “আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।” যা গল্পের রহস্যের চূড়ান্ত উন্মোচন ঘটায়।
গল্পে অশরীরী আত্মার ভর করার ঘটনাগুলি কেবল অলৌকিক নয়, মানবমনের অজানা গভীরতাকেও প্রকাশ করে — ব্যাখ্যা করো।
➤ উত্তর ➨ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘হলুদ পোড়া’ গল্পে অশরীরী আত্মার ভর করার মতো অলৌকিক ঘটনাগুলিকে নিছক ভৌতিকতার স্তরে আটকে রাখেননি, বরং সেগুলিকে মানবমনের চাপা অপরাধবোধ, অস্থিরতা এবং অবচেতন সত্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
প্রথমবার, নবীনের স্ত্রী দামিনীর উপর যখন শুভ্রার আত্মা ভর করে, তখন কুঞ্জ গুণীর ‘হলুদ পোড়া’ প্রক্রিয়ায় দামিনীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে— “আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা… বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।” এই জবানবন্দি দামিনীর ব্যক্তিগত নয়, বরং এটি শুভ্রার জীবনের নিপীড়িত সত্য এবং গ্রামীণ সমাজে ছড়িয়ে থাকা গুপ্ত সন্দেহের বহিঃপ্রকাশ, যা এক সম্মোহন বা হিপনোসিসের মতো প্রক্রিয়ায় (হলুদ পোড়া) প্রকাশিত হয়।
তবে মানবমনের গভীরতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় শিক্ষিত ধীরেন চাটুয্যের উপর বলাইয়ের আত্মা ভর করার ঘটনায়। সমাজের কটূক্তি ও অপমানে জর্জরিত ধীরেনের মনে তখন “ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য”। এই মানসিক পতনের সময় যখন তিনি পোড়া বাঁশ ডিঙোতে না পেরে “হিংস্র জন্তুর চাপাগর্জনের মত গম্ভীর আওয়াজে” কথা বলেন, তখন তাঁর ভেতরের লুকানো সত্যটি অশরীরীর বেশে বেরিয়ে আসে। ধীরেনকে যে আত্মা ভর করে, সে হলো বলাইয়ের আত্মা—যা তাঁর প্রতিশোধ বা খুনের অপরাধবোধের প্রতীক। এই ভর করার মধ্য দিয়েই ধীরেনের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা চরম সত্যটি প্রকাশ পায়— “আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।” এইভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখান, কুসংস্কারের আবরণে আবৃত এই অলৌকিকতা আসলে মনস্তাত্ত্বিক চাপ এবং অপরাধীর আত্ম-স্বীকৃতিরই নাটকীয় রূপ।
বলাই চক্রবর্তী ও শুভ্রার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে লেখক সমাজের কোন নৈতিক সংকটকে তুলে ধরেছেন?
➤ উত্তর ➨ বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্ব ও গ্রামীণ কুসংস্কারের বাস্তবানুগ চিত্রায়ণের জন্য বিখ্যাত। তাঁর লেখা ‘হলুদ পোড়া’ গল্পে বলাই চক্রবর্তী ও শুভ্রার জোড়া হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের নৈতিক সংকট, বিশেষত যুক্তির প্রতি চরম অবিশ্বাস এবং গুজবের কাছে আত্মসমর্পণের সংকটকে তুলে ধরেছেন।
গল্পে নৈতিক সংকটের প্রথম প্রকাশ ঘটে যখন দুটি খুনের বাস্তব কারণ অনুসন্ধানের চেয়ে গ্রামবাসী অলৌকিকতার আশ্রয় নেয়। বলাই চক্রবর্তী ছিল এমন একজন মানুষ যার “এই রকম অপমৃত্যুই আশেপাশের দশটা গাঁয়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল”, অর্থাৎ তার জীবনযাপনেই অনৈতিকতা ছিল। অন্যদিকে, শুভ্রার খুন ছিল রহস্যময়। এই দুই খুনের মধ্যে যখন “বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে” সম্পর্ক আবিষ্কার করা যাচ্ছিল না, তখন গ্রামবাসী গুণী কুঞ্জ মাঝিকে ডেকে পাঠায়। এই পদক্ষেপ ইঙ্গিত দেয় যে, গ্রামীণ সমাজ বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক (ধীরেনের পরামর্শ) পথে না গিয়ে অলৌকিক সমাধানকে নৈতিকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করে। শিক্ষিত ধীরেন যখন কুঞ্জকে ডাকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন— “ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন”—তখন তাঁর কথা কেউ শোনেনি।
খুনের রহস্যকে কেন্দ্র করে সমাজে মিথ্যা কলঙ্ক ও গুজবের নৈতিক সংকটটি সামনে আসে। শুভ্রার খুনের পর যখন দামিনীর উপর ভর করে শুভ্রার আত্মা “বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে” বলে, তখন বলাই তো আগেই মারা গেছে। এই জটিলতা সমাজের নৈতিক বিচারকে আরও শিথিল করে দেয়। বুড়ো ঘোষালের মতো মানুষ তখন যুক্তি দেন— “শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না?” অর্থাৎ, সমাজ খুনের নৈতিক দায়িত্ব ব্যক্তির ওপর না চাপিয়ে, তা অশরীরী বা ভৌতিক শক্তির ওপর চাপিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়। এই গুজবের কারণে শুভ্রার দাদা ধীরেন যখন অপমান ও ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে স্কুল থেকে বিতাড়িত হন, তখন সমাজের এই গুজবভিত্তিক অনৈতিক বিচার চূড়ান্ত হয়ে ওঠে। গল্পটি প্রমাণ করে, গ্রামীণ সমাজে সত্য এবং ন্যায়বিচারের চেয়ে অন্ধ বিশ্বাস ও লোকলজ্জা সম্পর্কিত ধারণাগুলিই নৈতিকতা নির্ধারণ করে।
হলুদ পোড়া’ গল্প অবলম্বনে ধীরেন চাটুয্যের চরিত্রের বিশ্লেষণ করো।
➤ উত্তর ➨ বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হলুদ পোড়া’ গল্পে ধীরেন চাটুয্যে চরিত্রটি যুক্তিবাদ ও অন্ধবিশ্বাসের সংঘাতের প্রতীক। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বোনের মৃত্যু ও শেষ পরিণতি চরিত্রটিকে গভীরতা দিয়েছে।
ধীরেন চাটুয্যে চরিত্রের বিশ্লেষণ
১. শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ: ধীরেন “ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ” করে স্থানীয় স্কুলে ভূগোল পড়াতেন। প্রথমে তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন, তাই দামিনীর অস্বাভাবিক আচরণকে “অসুখ” মনে করে কুঞ্জকে ডাকার বিরুদ্ধে নবীনকে বলেছিলেন— “ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন।”
২. সমাজ-সচেতন সংস্কারক: শিক্ষিত হওয়ার কারণে গ্রামের উন্নতি ছিল তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। তিনি “সাতচল্লিশখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী, সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি” প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও পরে “গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু’বছরে চারটি ছেলেমেয়ের জন্ম হওয়ায়” তাঁর উৎসাহে ভাটা পড়ে।
৩. ব্যক্তিগত শোক ও মানসিক অস্থিরতা: বোন শুভ্রার হত্যাকাণ্ডের পর তিনি তীব্র শোক ও অস্থিরতার মধ্যে পড়েন। খুনের রহস্য তাঁকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রাখে যে, মাঝে মাঝে “কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়।”
৪. সামাজিক অপমান ও একঘরে হওয়া: শুভ্রার খুন ও তাকে ঘিরে কলঙ্কের গুজবে ধীরেন সমাজে অপদস্থ হন। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে “একমাসের ছুটি” নিতে বললে তিনি নিজেকে “জীবন্ত ব্যঙ্গের মত” মনে করেন এবং “চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ী চলেছে।”
৫. যুক্তির পতন ও আত্মসমর্পন: ক্রমাগত অপমানে তাঁর যুক্তিবাদী মন ভেঙে পড়ে এবং তিনি কুসংস্কারের কাছে হার মানেন। তিনি বিশ্বাস করেন— “জীবিত ও মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় হলো সন্ধ্যা।” এই অন্ধবিশ্বাসই তাঁকে ঘাটের দিকে টেনে নিয়ে যায়।
৬. অপরাধবোধের প্রতীকী প্রকাশ: শেষে, পোড়া বাঁশের কাছে আটকে গিয়ে ধীরেনের মুখ দিয়ে বলাইয়ের আত্মা যখন বলে— “আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।”—তখন বোঝা যায়, বলাইকে খুন করার অপরাধবোধ ধীরেনের অবচেতন মনে কাজ করছিল। তাঁর চরিত্রটি সমাজের চাপ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সামনে শিক্ষিত মানুষের অসহায়তার প্রতীক হয়ে ওঠে।
‘হলুদ পোড়া’ গল্প অবলম্বনে ধীরেন চাটুয্যের স্ত্রী শান্তির চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। গ্রামীণ পরিবেশের ভয় ও কুসংস্কার তার চরিত্রে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
➤ উত্তর ➨ বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ‘হলুদ পোড়া’ গল্পে শান্তি চরিত্রটি গ্রামীণ সমাজে ভয় ও লোকবিশ্বাসের প্রতিভূ। তার চরিত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়:
ধীরেন-পত্নী শান্তি চরিত্রের বিশ্লেষণ
১. কুসংস্কারের শিকার গৃহবধূ: শান্তি ছিল একজন “গেঁয়ো একটি মেয়েকে” এবং তার মন সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন। সে ক্ষেন্তি পিসির কথামতো অশরীরী আত্মাকে আটকাতে আগা-মাথা পোড়ানো বাঁশ ব্যবহার করে।
২. চরম ভীরুতা ও আতঙ্ক: শুভ্রার খুনের পর সে তীব্র আতঙ্কে দিন কাটায়। সামান্য কারণে “আঁতকে ওঠে” এবং “পেঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল।”
৩. পারিবারিক নিরাপত্তার উদ্বেগ: ভয়ের মধ্যেও সে সন্তানদের রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। সে ছেলেমেয়েদের ঘরের মধ্যে “আটকে রাখে” এবং সন্ধ্যার পর একা বাইরে যেতে ভয় পায়।
৪. লোকবিশ্বাসে ভক্তি: অশরীরীকে তাড়াতে সে নিজের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনে। তার বিশ্বাস ছিল “এটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে”, তাই সে মাছ রান্না করা বন্ধ করে দেয় এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগেই প্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁখ বাজায়।
৫. শিক্ষিত স্বামীর বিপরীতে অবস্থান: যদিও তার স্বামী ধীরেন “ফিজিক্সে অনার্স পাশ” করা যুক্তিবাদী, তবুও শান্তি কখনোই তার যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিল না। সে স্বামীর যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে লোকাচারকেই প্রাধান্য দেয়।
৬. ঘটনার সাক্ষী ও বিশ্বাসীর ভূমিকা: গল্পের চরম মুহূর্তে সে স্পষ্ট শুনতে পায় ধীরেনের কণ্ঠে অশরীরীর স্বর— “ডিঙ্গোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।” এই ঘটনা শান্তির গ্রামীণ বিশ্বাসের সত্যতাকেই তার কাছে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।
‘হলুদ পোড়া’ গল্প অনুসারে বলাই চক্রবর্তী ও ধীরেনের বোন শুভ্রা কিভাবে খুন হয়েছিল — তা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।
➤ উত্তর ➨ বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘হলুদ পোড়া’ গল্পটি বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এটি একদিকে লোক-কথা মূলক গল্প আবার অন্যদিকে ভৌতিক আবহে মোড়ানো, যেখানে গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার, রহস্য, ভয় এবং মানুষের মনস্তত্ত্ব/মানসিকতা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
গল্পের শুরু হয় কার্তিক মাসে হঠাৎ ঘটে যাওয়া দুটো খুনের ঘটনাকে ঘিরে। প্রথমে খুন হন বলাই চক্রবর্তী, তিন দিন পর খুন হয় শুভ্রা।
বলাই চক্রবর্তীর হত্যাকাণ্ড: গল্পের প্রথমে বলাই চক্রবর্তীর খুন হয়। বলাই ছিল “মাঝবয়সী যোয়ান মদ্দ পুরুষ”। তাকে গাঁয়ের দক্ষিণের ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটি মরা গজারি গাছের নিচে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার মাথাটা আটচির হয়ে ফেটে গিয়েছিল, যা থেকে অনুমান করা হয়, তাকে খুব সম্ভবত অনেকগুলি লাঠির আঘাতে খুন করা হয়েছে। বলাই ছিল অনৈতিক চরিত্রের লোক, তাই তার এইরকম অপমৃত্যু গ্রামবাসীরা “প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনাও করছিল।”
শুভ্রার হত্যাকাণ্ড: বলাই চক্রবর্তীর খুনের ঠিক তিন দিন পর খুন হয় শুভ্রা। শুভ্রা ছিল “ষোল-সতের বছরের এক রোগা ভীরু মেয়ে” এবং সাত মাসের গর্ভবতী অবস্থায় সে বাপের বাড়ি এসেছিল। তার মৃত্যু নিয়ে গ্রামে হৈচৈ কম হলেও “মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না”, কারণ সে ছিল গেরস্ত ঘরের সাধারণ মেয়ে। শুভ্রাকে খুন করা হয় বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটে, যখন “সাঁঝের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে”। তাকে গলা টিপে মেরে রাখা হয়। অথচ কার্তিকের এক সন্ধ্যায় বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মতো নিরীহ মেয়েকে কে বা কারা গলা টিপে খুন করে গিয়েছিল, তা কেউ বুঝে উঠতে পারেনি। এমন নির্দয় এক ঘটনার সাক্ষী হয়ে এবং এর কারণ অনুসন্ধান করতে না পেরে ‘গাঁ শুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল।’ এই খুনের কারণ প্রথমে রহস্যময় থাকলেও, নবীনের স্ত্রী দামিনীর ওপর শুভ্রার আত্মা ভর করার মধ্য দিয়ে জানা যায় যে, তাকে “বলাই খুড়ো” খুন করেছে। অর্থাৎ, বলাই তার অনৈতিক কাজের জন্য শুভ্রাকে গলা টিপে খুন করেছিল এবং এই হত্যার প্রতিশোধ নিতেই পরে ধীরেন বলাইকে খুন করেন।
বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমন ভাবে জখম পর্যন্ত হয়নি, যখন হল পর পর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো। এই দুটি হত্যাকাণ্ডই গ্রামীণ সমাজে বাস্তব বিচারের পথ বন্ধ করে অলৌকিক রহস্য, গুজব ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিশোধের জন্ম দেয়।
‘হলুদ পোড়া’ গল্প অবলম্বনে গুণী কুঞ্জ মাঝির চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।
➤ উত্তর ➨ বাংলাসাহিত্যের বিখ্যাত কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্ব ও গ্রামীণ কুসংস্কারের বাস্তবানুগ চিত্রায়ণের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। তাঁর লেখা ‘হলুদ পোড়া’ গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের জগতে ভৌতিক ও লোককথা নির্ভর সাহিত্যের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার, রহস্য এবং মানুষের মানসিকতা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
গল্পে গুরুত্বপূর্ণ মূল চরিত্র গুলোর মধ্যে একটি অন্যতম চরিত্র হলো গুণী কুঞ্জ মাঝি হলো গ্রামীণ লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূর্ত প্রতীক। সে যুক্তিরহিত গ্রামীণ সমাজের প্রধান আশ্রয়স্থল।
গুণী কুঞ্জ মাঝির চরিত্র বিশ্লেষণ
১. পেশা ও সামাজিক পরিচয়: কুঞ্জ ছিল গ্রামের গুণী বা ঝাড়ফুঁককারী ব্যক্তি। তার মাধ্যমেই গ্রামের মানুষজন অলৌকিক সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজত। দামিনীর উপর শুভ্রার আত্মা ভর করলে শিক্ষিত ধীরেনের কথা অগ্রাহ্য করে গ্রামের সকলে বলে ওঠে— “কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।”
২. লোকবিশ্বাসের ধারক: কুঞ্জ তার কাজকর্মে লোকবিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে। দামিনীকে বশে আনতে সে প্রথমেই ঘোষণা করে— “ভর সাঁঝে ভর করেছেন সহজে ছাড়বেন না!”—যা মানুষের মনে ভীতি ও অলৌকিকতার ধারণা গেঁথে দেয়।
৩. হলুদ পোড়ার প্রয়োগ: তার রহস্য সমাধানের মূল পদ্ধতি ছিল ‘হলুদ পোড়া’। সে মন্ত্র পাঠ, জল ছেটানো এবং কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে সেই হলুদ দামিনী ও পরে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে সত্য উদ্ঘাটন করে।
৪. রহস্যের সূত্রপাত ও সমাধান: প্রথমে দামিনীর মুখ দিয়ে সে শুভ্রার খুনি হিসেবে বলাই চক্রবর্তীর নাম প্রকাশ করে। দ্বিতীয়বার, ধীরেন যখন বাঁশ ডিঙোতে না পেরে বিকৃত কণ্ঠে “বাঁশ সরিয়ে দাও” বলে, তখন কুঞ্জই তার পদ্ধতি প্রয়োগ করে বলাইয়ের আত্মার মাধ্যমে চরম সত্যটি প্রকাশ করে— “আমি বলাই চক্রবর্তী! শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।”
৫. নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টিকারী: কুঞ্জের উপস্থিতি গ্রামের মানুষকে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার স্বাদ দেয়। তার ঝাড়ফুঁকের পদ্ধতিগুলি গ্রামের মানুষকে “তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতুহল ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ” দেয়, যা ঘটনাটিকে এক প্রকার নাটকীয় প্রদর্শনীতে পরিণত করে।
৬. যুক্তির ওপর কর্তৃত্ব: কুঞ্জ চরিত্রটি প্রমাণ করে যে, গ্রামীণ সমাজে বিজ্ঞান ও যুক্তির চেয়ে অন্ধ বিশ্বাস ও অলৌকিকতার শক্তিই বেশি প্রবল। শিক্ষিত ধীরেনের আপত্তি সত্ত্বেও তার পদ্ধতির মাধ্যমেই সকলে খুনের রহস্যের সমাধান মেনে নেয়।
উচ্চমাধ্যমিক চতুর্থ সেমিস্টারের পরবর্তী ক্লাস এবং নোটগুলি পেতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকো, আর এটি অবশ্যই বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দাও।
আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রাম Study গ্রুপে যুক্ত হোন -